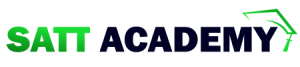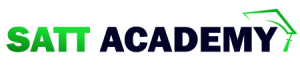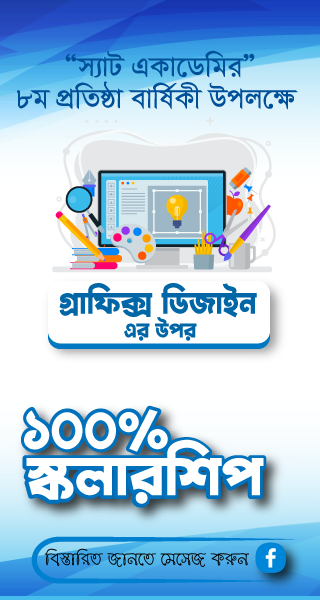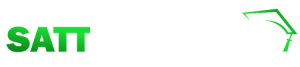সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য শিল্প নৃত্যগীতবাদ্য বুঝে থাকি। এগুলো সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ, তবে এগুলোই সংস্কৃতির সবটা নয়। সংস্কৃতি বলতে মুখ্যত দু'টো ব্যাপার বোঝায় : বস্তুগত সংস্কৃতি আর মানস-সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, আহারবিহার, জীবনযাপন প্রণালি— এসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর সাহিত্যে-দর্শনে শিল্পে-সংগীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বলা যায় মানস-সংস্কৃতি। বস্তুগত আর মানস-সংস্কৃতি মিলিয়েই কোনো দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে।
বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছি, তা অনেক পুরনো। এই সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে মেলে, কিছু বৈশিষ্ট্য আলাদা করে শনাক্ত করা যায়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে, ধর্মানুপ্রেরণায়, বর্ণপ্রথায়, উৎপাদন-পদ্ধতির অনেকখানিতে বাঙালি সংস্কৃতির মিল পাওয়া যাবে গোটা উপমহাদেশের সঙ্গে। বাংলাভাষা ইন্দো- ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা— এই গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে। বাংলার অনেক রীতিনীতিরও মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেই এলাকায়। আবার ধান-তেল-হলদি-পান- সুপারির ব্যবহারে মিল পাওয়া যায় দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে। সেলাইছাড়া কাপড় পরার বিষয়েও বেশি মিল ঐ এলাকার সঙ্গে। এর কারণ, বাংলার আদি জনপ্রবাহ ছিল প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠীসম্ভূত। পরে এর ওপরে আর্য জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রভাব এসে পড়ে। সে প্রভাব এত তীব্র ছিল যে, তাই দেশজ উপকরণে পরিণত হয়। পরে মুসলমানরা যখন এদেশ জয় করলেন, তখন তাঁরা যে সংস্কৃতি নিয়ে এলেন, তাতে তুর্কি-আরব-ইরান-মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশেল ছিল। সেখান থেকে অনেক কিছু এল বাঙালি সংস্কৃতিতে। তারপর এদেশে যখন ইউরোপীয়রা এলেন, তখন তাঁরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ ঘটালেন আরো একটি সংস্কৃতির। এভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে অনেক সংস্কৃতি- প্রবাহের দান এসে মিশেছে। আর নানা উৎসের দানে আমাদের সংস্কৃতি হয়েছে পুষ্ট।
বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিতে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দরুন বাংলায় বিভিন্ন রাজত্ব যেমন স্থায়িত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি বাংলার এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ধর্মমতের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও উদ্ভাবন দেখা দিয়েছে। বাংলার সাহিত্য-সংগীতের
ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য গান ভিত্তি করে লেখা মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব পূর্ব-বঙ্গের জলাভূমিতে, পশ্চিম-বঙ্গের রুক্ষ মাটিতে বিকাশ বৈষ্ণব পদাবলীর। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালি গানের বিস্তার, শুষ্ক উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়ার, আর বাংলা পশ্চিমাঞ্চলে কীর্তন ও বাউলের। শিল্পসামগ্রীর লভ্যতাও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল । তাই বাংলার স্থাপত্যে পাথরের চেয়ে ইট আর মাটির প্রাধান্য, মৃতফলক এখানকার অনন্য সৃষ্টি।
বাংলার ভাস্কর্যেও মাটির প্রাধান্য, আর সেই সঙ্গে দেখা যায় এক ধরনের সামগ্রীর ওপরে অন্য ধরনের সামগ্রীর উপযোগী শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস ।
অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলার মানস-সংস্কৃতি প্রধানত আশ্রয় করেছে সাহিত্য ও সংগীত, অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনকে। স্বল্প হলেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাংলার দান আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিতের সাধনার তেমন ঐতিহ্য বাংলায় গড়ে ওঠেনি ।
ফলিত বিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্রে— আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বাংলার একটা ভূমিকা ছিল, কিন্তু তাও ছিল সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল মূলত কারুশিল্পে। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই কারুশিল্প বিকশিত হলেও এর প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি । প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন হয়েছে ইংরেজ আমলে । তবে সে প্রযুক্তি বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে ধার করা।
বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে থাকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে। এই স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় শাসন-ব্যবস্থায়, সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও লিপির বিকাশ সে স্বাতন্ত্র্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। বহিরাগত মুসলমানরা এদেশ জয় করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে। মুসলমান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তার বিকাশে সহায়তা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মুঘলরা বাংলাদেশ জয় করেন। মুঘল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আগের মতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি, তবে একটা বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে তখন বাংলার সংস্কৃতির যোগ ঘটে। তারপর আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হলে যোগাযোগের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়; বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার যোগ সাধিত হয়।
ঐ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির কিছু কিছু ভেদ ছিল । কারুশিল্পের ক্ষেত্রে ভেদটা খুব চোখে পড়ে। এর একটা ধারা ছিল উচ্চ শ্রেণির ভোগ্য- রুপোর কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, রেশমী ও উঁচু মানের সুতি কাপড়ের শিল্প; অন্য ধারাটা ছিল সাধারণের ভোগ্য— শাঁখের ও পিতলের কাজ, নকশী কাঁথা, পাটি, আলপনা। সমাজে উঁচু পর্যায়ে সংস্কৃত বা ফারসির যে-চর্চা হতো তা নিচু স্তরকে স্পর্শ করে নি। ধ্রুপদী সংগীত ও লোকসংগীত চর্চার মধ্যেও এমনি পার্থক্য ছিল। লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের ভেদও ছিল। তবে বাংলার সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজের প্রায় সকল স্তরকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল। এইজন্যে বাংলার মানস-সংস্কৃতিতে সবচেয়ে প্রাধান্য সাহিত্য ও সঙ্গীতের।
ইংরেজ আমলে যে নতুন সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে, তার প্রেরণা এসেছিল প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে। পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগ ঘটেনি, তারা এর বিকাশে এবং এর উপভোগ্যতায়ও অংশ নিতে পারে নি। একালের সাহিত্য-সংগীত-নাটক-চিত্রকলা প্রধানত নগরের সৃষ্টি। এর অর্থ আমাদের মানস-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপ নির্মিত হয় উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিতের হাতে। ঔপনিবেশিক নয়, কিন্তু আগের মতোই শ্রেণিবিভক্ত। তাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সকলের অধিকার সমান নয় এবং এক শ্রেণির সৃষ্ট সংস্কৃতিতে অন্য শ্রেণির প্রবেশাধিকার নেই; আবার এক শ্রেণির সৃষ্ট সংস্কৃতি অন্য শ্রেণির পক্ষে রুচিকর নয়। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে এই অবস্থার কোনো বদল আশা করা যায় না ।
আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিকে এক অর্থে ধর্মমুখী বলা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্য, ইসলাম ধর্মবিষয়ক রচনা বা নবিজীবনী, কীর্তন বা শ্যামাসংগীত তার উদাহরণ । এমনকি অধ্যাত্ম-তত্ত্বাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যানও এর মধ্যে ধরা যায় । তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় । প্ৰথমত, বাংলার সাহিত্য ও সংগীতে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বক্তব্য একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মকলহের পাশাপাশি এক ধরনের সমন্বয়- চেতনা কাজ করেছে- যোগ ও সুফিবাদের সমন্বয় আর বাউল গান তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত, এর সবক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বস্তুর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানবিকতা। বৈষ্ণব কবিতা বা আধ্যাত্মিক প্রণয়কাহিনি তত্ত্বের চেয়ে প্রেমের কাহিনিরূপেই আদৃত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যে দেবতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষ। অবৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখেছেন, অমুসলমান কবি লিখেছেন কারবালা-কাহিনি ।
এই মানবিকতাকে যদি বাঙালি সংস্কৃতির একটা মুখ্য প্রকাশ বলে গণ্য করি, তাহলে উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিতে সেই মানববাদের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করি। পুরনো ধারার সংস্কৃতিতে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ আছে। একালের সংস্কৃতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা সরবে শোনা যায়। এই দিক দিয়ে দেখলে আমাদের সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় মানবকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। আমাদের সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ নিয়ে যেমন আমরা গর্ব করতে পারি, তেমনি তার এই ভাববস্তুও আমাদের গৌরবের বিষয়।
আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. এ.টি.এ.এম. মোয়াজ্জম, মাতা সৈয়দা খাতুন। ১৯৫১ সালে ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গবেষক ও প্রাবন্ধিক । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, পুরোনো বাংলা গদ্য, বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদকসহ প্রচুর সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০২০ সালের ১৪ই মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
প্রবৃত্তি- অভ্যাস, অভিরুচি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী- পৃথিবীর ভাষাসমূহকে তাদের উৎপত্তি অনুসারে কয়েকটি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী অন্যতম। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি প্রধান ভাষাগুলো এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নৃ-তাত্ত্বিক- জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত। আর্য নরগোষ্ঠী - প্রাচীন ইরাক-ইরান অঞ্চল থেকে আগত জনগোষ্ঠী। মনসামঙ্গল- মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস রচিত কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সাপের দেবী মনসার বন্দনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলি- মধ্যযুগে রচিত ভক্তিমূলক কবিতা। কবি জয়দেব বৈষ্ণবপদাবলির বিখ্যাত কবি। আয়ুর্বেদ- দেশজ চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ। কারুশিল্প - হস্তনির্মিত শিল্প যা একাধারে সুন্দর ও প্রাত্যহিক কাজে লাগে। সপ্তম- অষ্টম শতাব্দী-৬০০-৭০০ শতাব্দী। সুফিবাদ - মুসলিম ধর্মীয় মতবাদ বিশেষ।
বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের উৎসব (২০০৮) গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধটি সংকলিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। আদিকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে বিশ্বের নানা জাতির সংস্কৃতি। এতে আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে, বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিকে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। আর তা হলো আমাদের লোকসংস্কৃতি । আমাদের সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, মাটির ভাস্কর্য, কারুশিল্প, বয়ন শিল্পের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। মূলত ‘আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে বাঙালি ও বাংলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ প্রবন্ধ আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মানবিকতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিদ্রোহী ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।
আরও দেখুন...